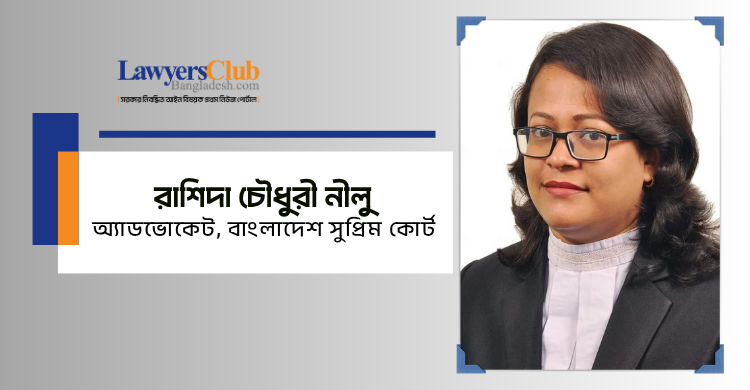রাশিদা চৌধুরী নীলু : বিচার বিভাগে হঠাৎ করে একযোগে ১৮ জন বিচারককে অবসরে পাঠানোর ঘটনাটি কেবল একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিয়ে এক নীরব কিন্তু গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি। একটি সুস্থ ও কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি হলো এর তিনটি মূল স্তম্ভ; আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগ। এই তিন স্তম্ভের পারস্পরিক ভারসাম্য এবং নিরপেক্ষতাই রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও জনগণের অধিকার সুরক্ষার মূল চাবিকাঠি। এর মধ্যে, বিচার বিভাগ একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নাগরিকদের শেষ আশ্রয়স্থল, যেখানে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হয়।
সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিধানগুলো স্পষ্টত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয়, যা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া অসম্ভব। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা মানে শুধু আলাদা ভবন নয়, মনোচিন্তা ও সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা। যখন এই বিচার বিভাগকে ‘অবসরের’ আড়ালে অন্ধকারে ঢেকে দেওয়া হয়, তখন তা কেবল কিছু ব্যক্তির কর্মজীবনের শেষ নয়, বরং পুরো গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর এক গুরুতর আঘাত, যা জনগণের আস্থায় ফাটল ধরায় এবং রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড দুর্বল করে তোলে।
সরকারি চাকরিতে ‘জনস্বার্থে অবসর’ একটি সুনির্দিষ্ট আইনি বিধান, যা সাধারণত অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই বিধানের উদ্দেশ্য হলো, যদি কোনো সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গুরুতর অসদাচরণ, অদক্ষতা বা দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট ও প্রমাণিত অভিযোগ থাকে, তবে রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে, ১৮ জন জ্যেষ্ঠ বিচারককে একযোগে অবসরে পাঠানো কেবল আইনগত নয়, বরং নৈতিক ও সাংবিধানিক প্রশ্ন উত্থাপন করে।
“জনস্বার্থে অবসর” কী?
বাংলাদেশের “প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্তি বিধিমালা, ২০১৮”-এর ধারা ৪৮(১) অনুযায়ী, সরকার চাকরিজীবী কোনো কর্মকর্তাকে “জনস্বার্থে” অবসর প্রদান করতে পারে। এই বিধানের উদ্দেশ্য হলো—যদি কোনো কর্মকর্তার কর্মদক্ষতা, আচরণ বা কার্যক্রম রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী হয়, তবে তাকে স্বাভাবিক সময়ের আগেই অবসরে পাঠানো যায়।
একজন বিচারকের ৩০-৩৫ বছরের দীর্ঘ এবং নিবেদিত কর্মজীবনের শেষে পদত্যাগ বা অবসর হওয়া উচিত অত্যন্ত সম্মানজনক, কৃতজ্ঞতাসূচক ও মর্যাদাপূর্ণ একটি বিদায়। তাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং সমাজে তাদের অবস্থানকে যথাযথ সম্মান জানানো রাষ্ট্রের কর্তব্য। অথচ এই ঘটনা যেন এক ধরনের নির্বাসন, যেখানে রাষ্ট্রীয় কৃতজ্ঞতা বা বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক সম্মাননার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। এটি অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শর্তাবলীর মধ্যেকার অস্পষ্টতা ও ভারসাম্যের অভাবকেও তুলে ধরে, যা বিচার বিভাগের সামগ্রিক স্বাধীনতার ওপর প্রভাব ফেলে।
বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৪(৪) অনুচ্ছেদ স্পষ্টত বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলে, যা রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তির অন্যতম। এই স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য বিচারপতিদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং অপসারণে একটি নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ পদ্ধতি থাকা অপরিহার্য। উচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল হলেও, অধস্তন আদালতের ক্ষেত্রে সেই স্বচ্ছতা এখনো প্রশ্নবিদ্ধ।
সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরি ও নিয়ন্ত্রণ সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। অন্যদিকে, ১১৬ অনুচ্ছেদ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের ওপর ক্ষমতা অর্পণ করে। এই অনুচ্ছেদগুলো বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার সাংবিধানিক নির্দেশনা দেয়।
যদি এই সিদ্ধান্ত নির্বাহী বিভাগের ইচ্ছাধীন হয়ে থাকে, তবে তা সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের চেতনার পরিপন্থী, যা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার মূলে আঘাত হানে। বিচারকদের চাকরির শর্তাবলী, যেমন বিচার বিভাগীয় সেবা আইন, ২০০৭-এর অধীনে ‘জনস্বার্থে অবসর’ এর অপপ্রয়োগ বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করতে পারে এবং বিচারিক কার্যক্রমে নির্বাহী বিভাগের প্রভাব বাড়াতে পারে।
প্রশাসনিক হাতিয়ার
‘জনস্বার্থে অবসর’ দেওয়ার ক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক হাতিয়ার, যা সুনির্দিষ্ট আইন ও বিধির অধীনে ব্যবহৃত হওয়ার কথা। এর মূল লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রের বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং অদক্ষ বা বিতর্কিত কর্মকর্তাদের অপসারণ করা। কিন্তু যদি এর ব্যবহার পক্ষপাতদুষ্ট হয়, বা রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এটি রাষ্ট্রীয় শুদ্ধাচারের পরিবর্তে ‘নির্বিকার প্রতিশোধের’ হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে। পূর্বের ইতিহাসেও এমন নজির বিদ্যমান, যেখানে সরকারের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণকারী বা ‘অবাধ্য’ আমলাদের আকস্মিকভাবে ‘জনস্বার্থে অবসর’ নামক কৌশলে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা কেবল ব্যক্তিবিশেষের কর্মজীবন নষ্ট করে না, বরং পুরো প্রশাসনিক কাঠামোতে ভয়, অস্থিরতা এবং আনুগত্যের সংস্কৃতি তৈরি করে।
প্রশ্ন এসে যায়, এই ১৮ জন বিচারকের কেউ কি এমন মত প্রকাশ করেছিলেন, যা সরকারের নীতি বা কাঠামোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল? কেউ কি স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনায় ‘অতিরিক্ত সাহসী’ ছিলেন, যা শাসকগোষ্ঠীর কাছে অপ্রীতিকর মনে হয়েছিল? যদি এমনটাই ঘটে থাকে, তাহলে এটি কেবল ক্ষমতার অপব্যবহার নয়, বরং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ, যা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী এবং আইনের শাসনের ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এটি বিচারকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব তৈরি করে এবং তাদের নিরপেক্ষভাবে রায় দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।
যদি বিচারকেরাই ভয়ে থাকেন, যদি প্রতিটি রায় দেওয়ার আগে তাদের ভাবতে হয়, “এটা কি কাউকে অখুশি করবে? এর ফলস্বরূপ আমার চাকরির কী হবে?” তাহলে সেই রায় আর ন্যায়বিচার নয়, বরং এক আত্মসমর্পণের দলিল। এই একযোগে অবসরের সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ বিচারকদের মনে কী বার্তা দেয়? এই বার্তা যদি হয় যে, শক্তি-ক্ষমতার কাছে মাথা নত না করলে অবসরের নামে বিদায় নিতে হবে, তবে বিচার বিভাগের ভবিষ্যৎ চরম অনিশ্চয়তায় পড়বে। এটি এমন একটি বিচারিক সংস্কৃতি তৈরি করবে, যেখানে বিচারকরা সরকারের আনুকূল্য লাভের চেষ্টা করবেন, যা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় বাধা।
ন্যায়বিচারের আলো নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে, অন্ধকার শুধু আদালতেই নয়, সমস্ত সমাজে ছড়িয়ে পড়বে। আর সেই অন্ধকারে হারিয়ে যাবে গণতন্ত্রের শেষ প্রদীপও।
‘রাষ্ট্রের আদর্শিক প্রতিভূ’
একটি রাষ্ট্রের অগ্রগতি এবং গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থার ওপর নির্ভরশীল। বিচারকগণ রাষ্ট্রের চাকরিসূত্রে নিযুক্ত হলেও, তারা ‘রাষ্ট্রের আদর্শিক প্রতিভূ’ এবং নাগরিকদের শেষ আশ্রয়স্থল। যদি জনগণ দেখে যে বিচারকরাও সরকারের অনুগ্রহ বা অসন্তুষ্টির শিকার হচ্ছেন, তাহলে তারা কাকে ভরসা করবে? কিভাবে বলবে, “আদালত আমাদের শেষ ভরসা।” এই আস্থার সংকট যদি গভীরতর হয়, তবে গণতন্ত্রের শিকড় দুর্বল হয়ে পড়ে, জন্ম নেয় অনাস্থা, অবিশ্বাস এবং এক ধরনের সামাজিক ভীতি।
সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ব্যাহত হলে এই মৌলিক অধিকার কার্যকরভাবে সুরক্ষিত হতে পারে না। নাগরিক, যারা এই রাষ্ট্রের ভেতরে বসবাস করে, তাদের কাজ হচ্ছে প্রশ্ন তোলা। কারণ প্রশ্ন তোলা মানে অরাজকতা নয়; বরং গণতন্ত্রের জীবনীশক্তি। এটি একটি নাগরিক দায়িত্ব।
১৮ জন বিচারকের এই অবসরের ঘটনাটি যদি সত্যিই জনস্বার্থে হয়ে থাকে, তবে সেই ‘জন’ যেন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা পায়। সেই ‘জন’ যেন জানে, এই অবসরের পেছনে কী যুক্তি কাজ করেছে, কোন ধরণের অসদাচরণ বা অদক্ষতার কারণে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ কেবল সংবিধানের একটি অংশ নয়, এটি আমাদের সকলের মৌলিক অধিকারের রক্ষাকবচ। যে বিচারক রায় দেবার আগে ভাবেন, উনি কী হারাবেন, তিনি আর ন্যায়বিচার দিতে পারেন না। যে রাষ্ট্র ন্যায়বিচারকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, সে আসলে নিজের শেকড়েই কুঠার চালায়। ন্যায়বিচার তখনই সম্ভব, যখন বিচারকরা শুধু আইন ও বিবেকের কাছে জবাবদিহি করেন, ক্ষমতা বা প্রভাবের কাছে নয়।
লেখক : রাশিদা চৌধুরী নীলু; আইনজীবী, আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।