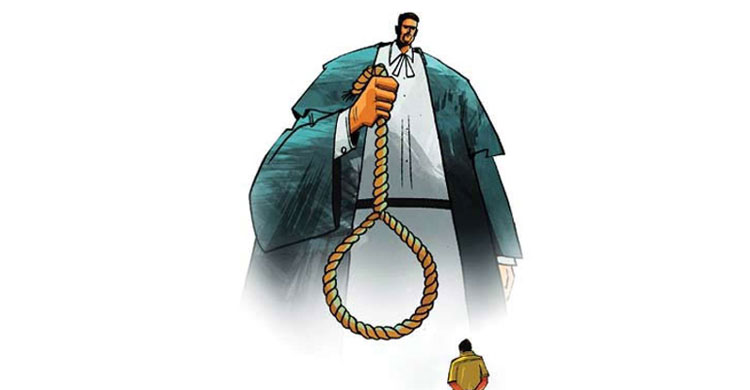হেলাল মহিউদ্দীন:
কানাডায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই। কানাডার নাগরিক হোক বা আশ্রিত যে কেউ হোক, কানাডার বাইরে অন্য কোনো দেশেও যদি তার মৃত্যুদণ্ডের সম্ভাবনা থাকে, কানাডা তাকে ফেরত দেবে না। অন্য দেশে কানাডীয় কেউ মৃত্যুদণ্ডিত হলে কানাডা রাষ্ট্রিয়ভাবে সাধারণ ক্ষমা চাওয়ার কূটনীতি চালিয়ে যেতেও আইনত বাধ্য।
কানাডার আইনানুগ বাধ্যতার পেছনে আছে একটি ঘটনা। ১৯৮২ সালে অ্যালেন স্মিথ নামের এক কানাডীয় মন্টানার দুজন আদিবাসীকে হত্যা করেন। মন্টানার আদালত তাঁকে মৃত্যদণ্ড দেন। মৃত্যুদণ্ডটি ব্যাপক বিতর্ক জন্ম দিয়েছিল। কানাডা কেন সেই মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন করতে পারল না বা চেষ্টা করল না তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় ২০০৭ সালে। সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী স্টকওয়েল ড্যে রক্ষণশীলদের নীতি কী হতে পারে জানালেন। বললেন, অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশের যেগুলোতে ‘আইনের শাসন’ আছে, সেই সব দেশে অপরাধ করে কোনো কানাডীয় সেই সব দেশের আইনে দণ্ডিত হলে কানাডার সরকার দণ্ডের বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থান নেবে না। নাগরিকেরা তাদের রাষ্ট্রের এই অবস্থান মোটেই পছন্দ করেনি। প্রতিবাদের ঝড় উঠল। ২০০৯ সালে উচ্চ আদালত রায় দিল অন্য দেশে হলেও কানাডাকে নৈতিক ও মানবিক অবস্থান হতেই মৃত্যদণ্ডবিরোধী কূটনীতি সক্রিয়ভাবেই চালিয়ে যেতে হবে।
গত বছর থেকে কানাডায় আম-নাগরিকদের মধ্যে আবার মৃত্যদণ্ড নিয়ে কথা বলাবলি শুরু হয়েছে। সীমিত আকারে হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মৃত্যদণ্ডের বিধানের ব্যতিক্রম বা ব্যত্যয় করা যায় কি না, এই আলাপ চলছে। পেছনের কারণ ব্রুস ম্যাকআর্থার নামে এক ঠান্ডা মাথার সুচতুর সিরিয়াল কিলার। পেশায় বহির্বাটি-বিন্যাসকারী (ল্যান্ডস্কেপার) ৬৭ বছর বয়সী ব্রুস ২০০৭ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত আটজন পুরুষকে হত্যা করেন। ব্রুসের হত্যাকাণ্ড যে নাগরিক চিন্তার জন্ম দিয়েছে, সেটি এই রকম—মৃত্যদণ্ড রহিতই থাকুক, কিন্তু ‘ঠান্ডা মাথা’য় ‘সুপরিকল্পিত’ ‘সজ্ঞান’ ‘নৃশংস’ হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের জন্য অন্তত এক-আধটি মৃত্যুদণ্ড রাখা যায় কি না? শুধুই ‘এক্সেমপ্লারি’ বা ‘দৃষ্টান্তমূলক’ করে হলেও ১০ বছরে একটি মৃত্যুদণ্ড হলেও না হয় এক-আধটি ব্যতিক্রম থাকতে পারে কি না?
ইউরোপের দেশগুলোতেও মৃত্যুদণ্ডপ্রথা রহিত। বিস্ময়ের বিষয় সেই সব দেশেও নৃশংসতার উদ্দেশ্য, ধরন ও মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে সীমিত আকারে, ব্যতিক্রম ও ‘দৃষ্টান্ত’ হিসেবে দু-একটি মৃত্যুদণ্ডের বিধান বলবৎ করা যায় কি না, সেই আলাপটি জোরালো হচ্ছে। বাংলাদেশে নুসরাত হত্যাকাণ্ডের রায় হওয়ার পর এই প্রসঙ্গটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে।
ধরা যাক, রাগারাগি বা ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে একজন অন্যজনকে মাথায় আঘাত করল। আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিহত হলো। এই হত্যাকান্ড এবং ঠান্ডা মাথার সুপরিকল্পিত হত্যাকান্ড তো আসলেই এক নয়। নুসরাতের হত্যাকান্ডটি যেমন শুধু নৃশংসই নয়, অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। তাতে নানা রকম ছক কাটা। ঘাতকদের বেঁচে যাওয়ার পথঘাট তৈরি করা। ক্ষমতার দানবীয় ব্যবহারের ব্যাকরণও আছে তাতে। রায় ঘোষণার দিন আদালতে যাওয়ার পথেও হত্যাকারী সিরাজের মুখে হাসি ছিল। বিচার চলাকালেও আসামিদের কেউ কেউ বাদীর পরিবারকে নির্দ্বিধায় হুমকি দিয়ে গেছেন। তাঁদের অনুমান ছিল ‘খুঁটির জোরে’ তাঁরা বেঁচে যাবেন। তাঁদের পেছনে রাজনৈতিক ক্ষমতার কলকাঠি নাড়ানোর শক্তিধারীরা ত্রাতা হয়ে আসবেন।
নুসরাত হত্যার রায় ঘোষণার পর মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে-বিপক্ষে বাংলাদেশে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই বিতর্কটি অত্যন্ত ইতিবাচক। সেই জন্য বিতর্কটি চলতে থাকা প্রয়োজন। আপাতত পক্ষে-বিপক্ষে ঢালাও বিতর্কটি চলছে। একদল বলছে ‘মৃত্যুদণ্ড থাকা দরকার’, অন্যদল বলছে ‘মৃত্যুদণ্ড রহিত হওয়া দরকার’। সবারই পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি আছে। বলা বাহুল্য, মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে যুক্তিগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। যেমন পৃথিবীতে মাত্র ৫৬টি দেশে মৃত্যদণ্ড বহাল আছে। ১০৬টি দেশেই দণ্ডটি রহিত, ২৮টি দেশে কাগজে-কলমে উপস্থিতি থাকলেও প্রয়োগ নেই-ই বলা যায়। ইউরোপীয় কমিশনভুক্ত ৪৪টি দেশ মানবিক অধিকার কনভেনশনের ১৩ ধারায় স্বাক্ষর করেই মৃত্যুদণ্ড রহিত করেছে। বাকি মাত্র তিনটি দেশ আর্মেনিয়া, রাশিয়া ও আজারবাইজান চূড়ান্ত সম্মতি সনদে স্বাক্ষর না করলেও নীতিগতভাবে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগের পক্ষে নয়। যুদ্ধাপরাধ বা দেশদ্রোহিতা বা অন্য দেশের পক্ষ হয়ে স্বদেশের বিরূদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি ও হত্যাকাণ্ডে নিযুক্ত থাকলে যেন উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যায়, সেই জন্যই তারা চূড়ান্ত সনদে স্বাক্ষর করেনি।
মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে আরও শক্তিশালী যুক্তি হচ্ছে, যেসব দেশে মৃত্যুদণ্ড বহাল আছে সেগুলোতে হত্যাকাণ্ডের মতো অপরাধ অন্য সব দেশের চেয়ে অনেক বেশি। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন, ভারত, কোরিয়া, তাইওয়ান, উত্তর কোরিয়া, হংকং ইত্যাদি দেশ এবং মুসলিম দেশুগুলো মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছে। ৫৬টি দেশের মধ্যে ৫৫টিতে যত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, বাকি একটিতে তার চেয়ে বহু বেশি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দেশটির নাম চীন। উত্তর কোরিয়ায় যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা কতটি ঘটে, তা জানার উপায়ই নেই তথ্যপ্রবাহে বিধিনিষেধ ও কড়াকড়ির কারণে।
দেশগুলো মৃত্যুদণ্ড রহিতকরণ বিলে স্বাক্ষর করে না কেন? উত্তর—হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল কিংবা নানা রকম রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য। তাতে অনেক নিরপরাধ মানুষ অন্যায় হত্যাকাণ্ডের অপব্যবহারের বলি হন, অপরাধ কমে না। নুসরাত হত্যার রায় সম্পর্কেও অনেকে মত জানাচ্ছেন যে এটি একটি পপুলিস্ট রায় বা লোকরঞ্জনমূলক রায়। রায় থেকে রাজনৈতিক ফায়দা আসবে। ক্ষমতাসীনদের প্রতি অনাস্থা কমবে। হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় দেশে যে ব্যাপক আবেগপ্রবণ ও মানবিক প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল, তার প্রতি রাষ্ট্রীয় সমর্থনটিও দেখানো যাবে। সাধারণ্যে সুবিচারহীনতার কারণে যে ক্ষোভ বা বিচারব্যবস্থার প্রতি যেরকম আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে, সেটিরও প্রশমনের সুযোগ হবে ইত্যাদি।
হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক ব্যবহারই বেশি হয়—হত্যাকাণ্ডের বিপক্ষে যাঁরা দাঁড়ান, তাঁদের একটি যুক্তি অবশ্যই সবল যে ষাটের দশকের শুরুতে বিশ্বময় মৃত্যুদণ্ডবিরোধী আন্দোলনের সূচনার পেছনে এটিই ছিল বড়সড় নিয়ামক। ১৯৬২ সালের ১১ ডিসেম্বর যেদিন কানাডার সর্বশেষ দুজন দণ্ডিত আর্থার লুকাস এবং রোনান্ড টুপিনকে ফাঁসি দেওয়া হয়, সেই দিন ফাঁসির মঞ্চের অদূরে জড়ো হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। তারা স্লোগানে স্লোগানে মুখর হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের নাম দিয়েছিল ‘রাষ্ট্রীয় হত্যাকান্ড’। লুকাস ও টুপিন রাজবন্দী ছিলেন না। তবু প্রতিবাদী বক্তাদের ভাষণজুড়ে একটি আশঙ্কাই ছিল যে অতীতে যেমনটি হয়েছে ভবিষ্যতেও ব্যক্তিগত অপরাধের শাস্তিসীমা ছাড়িয়ে ‘রাষ্ট্রীয় হত্যাকান্ড’টি অপব্যবহৃত হবে বেশি।
মৃত্যুদণ্ডবিরোধীরা এই আশঙ্কার সপক্ষে আর একটি দৃঢ়তর যুক্তি দেখান। যুক্তিটি এই যে প্রায় সব মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি ‘ক্লেমেন্সি’র ব্যবস্থা থাকে। যেটিকে আমরা ‘নির্বাহী রাষ্ট্রীয় ক্ষমা’ বা ‘দণ্ড লঘুকরণ’ বলি। সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানীরা আইনচিন্তার চেয়ে সমাজচিন্তায় বেশি জোর দেন বলে মৃত্যুদণ্ডবিরোধীদের এই যুক্তিকে ভালোভাবেই আমলে নেন। বাংলাদেশের বর্তমান ও বিগত ২ জন রাষ্ট্রপতিও ২৯ জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তা–ও সরাসরি ‘ক্ষমা’, দণ্ড লঘুকরণও নয়। এদের মধ্যে প্রমাণিত দাগি ভয়ংকর সন্ত্রাসীও আছে। ক্লেমেন্সিও প্রশ্নসাপেক্ষ—ক্ষমার জন্য যদি কোনো কারণ দেখানোই হয় তবে আগে কেন নয়, রায়ের পরে কেন? এখন কোথাও আর রাজতন্ত্র নেই। তাহলে রাজতন্ত্রের (রাজার সর্বোচ্চ ক্ষমতা) চর্চাই বা থাকবে কেন? নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ আইন অপব্যবহার নয় কি? প্রকারান্তরে বিচারব্যবস্থার ওপর এক্সট্রা-জুডিশিয়াল বা আইনবহির্ভূত হস্তক্ষেপ নয় কি? রাজনৈতিক সুবিধা বা ক্ষমতাধারীদের প্রতি পক্ষপাতের প্রয়োজনেই ক্লেমেন্সি ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ বেশি।
সচরাচর ক্লেমেন্সির কারণ বলা হয় ‘মানবিকতা বিবেচনা’! কিন্তু কার মানবিক বিবেচনায়? যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ২৮৮ জন ক্লেমেন্সি পেয়েছেন। শুধু ইলিনয়েই পেয়েছেন ১৮৭ জন। মার্কিন ক্লেমেন্সি খুবই নিয়ম-কানুন মানা এবং তথ্য-প্রমাণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা বা ইন্দোনেশিয়ায় অথবা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে? ইসলামে শরিয়া আইনে ‘কেসাস’ বলে একটি ক্লেমেন্সির ধারণা আছে। শুধু হত্যাকাণ্ডে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তরা ছাড়া অন্য কেউ ক্লেমেন্সি দিতে পারেন না। স্বামীর হত্যাকারীকে স্ত্রী ক্ষমা করে দিলে বা সন্তানসন্ততি ক্ষমা করে দিলেই শুধু ক্ষমা সম্ভব। নয়তো হত্যাকারীর শাস্তি হত্যাই। মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মীয় কারণে তাই মৃত্যুদণ্ড রহিত করার সুযোগ নেই। তবুও অসংখ্য মুসলিমই আছেন মৃত্যুদণ্ডবিরোধী কিংবা অন্তত কেসাস চর্চা বাড়িয়ে সীমিত মৃত্যুদণ্ডের পক্ষপাতী। বাংলাদেশ মুসলিম-প্রধান, সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং ক্লেমেন্সি প্রয়োগে রাজতন্ত্রীধর্মী। এই বৈপরীত্যগুলো নিয়ে কখনো কথা উঠেছে বলে মনে পড়ছে না।
কানাডায় ১৯৬২ তে শুরু হওয়া মৃত্যুদণ্ডবিরোধী বিতর্কটি চলেছিল টানা ১৫ বছর। ১৯৭৬ সালে সি-৮৪ বিলের মাধ্যমে কানাডা আইন করে মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্ত করে। মজার বিষয় হচ্ছে, এই ১৫ বছরে আইন থাকা সত্ত্বেও কাউকে নতুন করে মৃত্যদণ্ড দেওয়া হয়নি। জনগণের একটি অংশ ৮০–এর দশক থেকে আবারও ‘মৃত্যুদণ্ড পুনর্বহাল’–এর দাবি তোলে। ১৯৮৭ তে পুনর্বহালের বিলটি সংসদে পর্যালোচিত হয়, কিন্তু পাস হয়নি। ১৯৯৮ সালে বরং সম্পূর্ণই তিরোহিত করা হয়। সেনা আইন থেকেও মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্ত হয়। অর্থাৎ যুদ্ধকালীন হত্যা, দেশদ্রোহিতা, সেনাবিদ্রোহ এই সব ঘটলেও ঘটুক, কিন্তু ‘রাষ্ট্রীয় হত্যাকান্ড’ চলবে না। এই অগ্রগতিগুলোর কারণ, মৃত্যুদণ্ডবিরোধীরা থেমে থাকেননি। চীন, উত্তর কোরিয়া ও সমাজতান্ত্রিক বলয়ের দেশগুলো থেকেই শুধু নয়, অকাট্য যুক্তি হাজির করেন ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ভারত ইত্যাদি এবং সামরিক শাসনভুক্ত দেশগুলোতে মৃত্যুদণ্ডের বাড়বাড়ন্ত রাজনৈতিক ব্যবহার থেকেও। ইউরোপের চিত্রও প্রায় একই রকম।
প্রশ্ন উঠতে পারে, এত দীর্ঘ আন্দোলন এবং এতটা অগ্রগতির পর তাহলে এখন কেন আবার সীমিত মাত্রায় হলেও মৃত্যুদণ্ড পুনর্বহালের দাবি উঠছে কানাডার মতো দেশে বা ইউরোপের দেশগুলোতে? আসলে এসবই সামাজিক পরিবর্তনের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অপরাধের ধরন পাল্টায়, মাত্রা পাল্টায়, হিংস্রতা ও ভয়াবহতায় নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়। পাল্লা দিয়ে অপরাধের প্রতি জনপ্রতিক্রিয়া এবং প্রতিরোধচিন্তাও পাল্টায়। এই সবের কিছুই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া নয়। তবে প্রতিক্রিয়াগুলোতে সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানীরা অপরাধ-সম্পর্কিত জনমানস বিশ্লেষণের রসদ পেয়ে যান। এ জন্য বিতর্ক যুগ যুগ ধরে চালু থাকা প্রয়োজন।
নুসরাত হত্যাকাণ্ডের রায়ের পর পাওয়া তাৎক্ষণিক জনপ্রতিক্রিয়াই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া নয়। যাঁরা রায়ে তাৎক্ষণিক আনন্দ প্রকাশ করেছেন, তাঁরা যে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে এককাট্টা এমনটি বলা যায় না। দু–এক দিন গেলে তাঁরাও আস্তে আস্তে ভাবতে শুরু করবেন যে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অনেকেই তো পরিস্থিতির শিকার। তাঁরা বয়সে অপরিপক্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম ছিল কিংবা অন্য কোনো ছোটো অপরাধ ঢাকতে গিয়ে হত্যাকাণ্ডে জড়িয়েছেন। যাঁদের সামনে অনন্ত সময় পড়ে আছে, তাঁদের বিষয়ে হয়তো অনেক মতামতই নমনীয় হবে। বিজ্ঞ শীর্ষ আদালতের রায় এখনো বাকি। আশা করা যায়, শাস্তি লঘুকরণ বা রায় পরিবর্তনে শীর্ষ আদালতের রায়ে আরও সূক্ষ্ম বিবেচনার প্রকাশ ঘটবে। জনস্তুতির প্রতি পক্ষপাতমূলক রায় হবে না। রায়ের পর রাষ্ট্রপতির ক্লেমেন্সি থাকবে না। আর এই সব কিছুর দরকারেই বিতর্ক জারি রাখা অত্যাবশ্যক। মত-প্রতিমতের মধ্যেই ন্যায়বিচারের ও ন্যায্যতার সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে।
লেখক: নৃবিজ্ঞানী, কানাডার মানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো। সৌজন্যে: প্রথম আলো