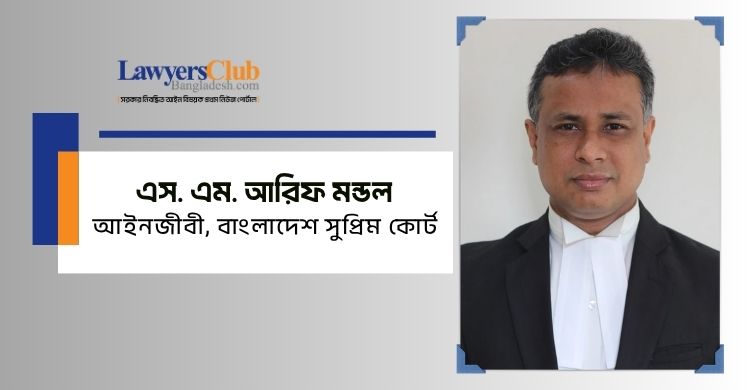এস. এম. আরিফ মন্ডল : Complete Justice বিষয়ে বাংলাদেশ সংবিধানের ১০৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। একমাত্র বাংলাদেশের আপীল বিভাগ এই অনুচ্ছেদের অধীন আদেশ প্রদান করতে পারে। যখন কোন মামলা বা বিষয়ে বাংলাদেশ সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপিলের কার্যধারা আপীল বিভাগে নিষ্পন্নধীন থাকে এবং যেখানে বিদ্যমান আইনে আপিলকারীর প্রতিকার লাভের সুযোগ থাকে না তখনই সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার এর ভিত্তিতে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়। যখন আদালত দেখতে পায় যে- আপিলকারীর কোন প্রতিকার নেই, যদিও নিজের কোন ভুল অথবা দোষ ছাড়াই তার প্রতি চরম অবিচার করা হচ্ছে।
যেখানে তথ্যগত বিষয় নিয়ে পক্ষদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, সেখানে পূর্ণ ন্যায়বিচারের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় । পক্ষগুলিকে নিজেদের মধ্যে আরও মামলার দিকে ঠেলে না দেয় তাহলে -এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে। সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের জন্য যেকোনো অসাধারণ পরিস্থিতিতে এই ক্ষমতার প্রয়োগ একটি সহজাত এবং পূর্ণাঙ্গ। এই ক্ষমতা প্রয়োগ আপীল বিভাগের একান্ত স্ববিবেচনার বিষয়। ব্যাপক বিবেচনার ভিত্তিতে আদালত এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
বিচারিক বিবেচনা হল দুই বা ততোধিক বিকল্পের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার ক্ষমতা, যেখানে প্রতিটিই আইনত বৈধ। সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার একটি সার্বিক ক্ষমতা যাহা সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যর্থতার কারণে অথবা ভাষাগত সীমাবদ্ধতার কারণে ন্যায়বিচারের সঠিক নির্দেশনা নিশ্চিত করে। সমতা, ন্যায়বিচার এবং সুবিবেচনা থেকে এই ক্ষমতার উদ্ভব হয়েছে।
বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১০৪ অনুযায়ী-কোন ব্যক্তির হাজিরা কিংবা দলিল উদ্ঘাটন বা দাখিল করিবার আদেশসহ আপীল বিভাগের নিকট বিচারাধীন যে কোন মামলা বা বিষয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয় হইতে পারে উক্ত বিভাগ সেইরূপ নির্দেশ,আদেশ, ডিক্রি বা রিট জারি করিতে পারিবেন।
সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আপীল বিভাগ যেসব নীতি অনুসরণ করে থাকে
যদি কোন উল্লেখযোগ্য এবং গুরুতর অবিচার হয়, অথবা যদি বিশেষ এবং ব্যতিক্রম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে আপীল বিভাগ সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার জন্য এই অসাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। আইন কে উপেক্ষা করে একজনকে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার দেয়া যাবে না এবং অন্য পক্ষকে বিদ্যমান আইনের যে সুবিধা আছে তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। কোন পক্ষ যদি আইনত মূল্যবান অধিকার অর্জন করে থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেই বিষয়টি উপেক্ষা করা যাবে না। যদিও আপীল বিভাগের এই ক্ষমতা আপাত দৃষ্টিতে অনেক বিস্তৃত এবং এর কোন সীমারেখা নেই।
আরও পড়ুন : ডিজিটাল সাক্ষ্য–সংক্রান্ত শেষ পর্ব: ভার্চুয়াল শুনানি ও সাক্ষ্যগ্রহণের প্রক্রিয়া
তবে আদালতে এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন আদেশ দিতে পারে না। এই ক্ষমতার কিছু অন্তর্নিহিত সীমারেখা রয়েছে-প্রথমত: এই ক্ষমতার অধীন কোন আদেশ বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বারা নিশ্চিতকৃত মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হবে না, দ্বিতীয়তঃ আপীল বিভাগ এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন মূল আইনের বিধানগুলিকে এড়িয়ে যেতে পারবেনা । তৃতীয়তঃ সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের নামে আপীল বিভাগ এমন প্রতিকার দিবেন না যাহা প্রথম আদালত তথা সংশ্লিষ্ট বিচারিক আদালত দিতে পারে না।
তবে বলা চলে- সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের অপ্রতুলতায় আপীল বিভাগ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। আদালতের এই ক্ষমতা শুধু বিচার প্রশাসনকে নিশ্চিত করে না, চরম অবিচার থেকেও রক্ষা করে। এই ক্ষমতা প্রয়োগে আদালতের কাছে যদি প্রতিমান হয়- সে নিজের আদেশ সু্য়ো মটু ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে পারেনি।আপীল বিভাগ সাধারণত যুগোপৎ তথ্য অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করে না, তবে পরিস্থিতির প্রয়োজন হলে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হস্তক্ষেপ করতে পারে।
আদালত এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রতিকার এক আইনে প্রদান করতে পারে, যদিও অন্য আইনের অধীন আবেদন করা হয়েছে। একতরফা কার্যধারায় বিশাল জরিমানার আদেশ প্রদান করা হলেও আদালত এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। মামলা দায়েরের পরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বা ঘটনা অনুসারে প্রতিকার প্রদান করতে পারে।যখন যোগসাজস ও জালিয়াতির মাধ্যমে কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আদালত থেকে অবৈধ আদেশ বা নির্দেশনা, ডিক্রি কেউ লাভ করে -আপীল বিভাগ তখন চোখ বন্ধ করে নিরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আপীল বিভাগ তখন সেই বেআইনি ডিক্রি বাতিল করতে পারে।
১০৪ অনুচ্ছেদ বলে আদালত যে সকল আদেশ দিতে পারে
১. আপিল বিভাগ এই ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে তার নিজস্ব আদেশ স্পষ্ট করতে পারেন।
২. হাইকোর্টের দেওয়া রায়ে কিছু অংশ মুছে ফেলতে পারেন।
৩. বিচারিক আদালতে মামলাটি আবারও শুনানির জন্য প্রেরণ করতে পারেন।
৪. কারিগরী কারণ উপেক্ষা করতে পারে- যেমন তামাদি বিষয়ে নিষ্পত্তিতে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।
৫. এমন কোন নথি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করতে পারে যা হাইকোর্ট বিভাগে গ্রহণ করা হয়নি।
আপীল বিভাগের সাম্প্রতিক এই ক্ষমতা প্রয়োগ
কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মামলা বা দরখাস্ত দায়ের করতে তামাদির প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়। আপীল বিভাগ সংবিধানের ১০৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে সাধারণ আইন এবং বিশেষ আইনের অধীন তামাদির মেয়াদ বৃদ্ধি করেছিল। চিপ ইঞ্জিনিয়ার সড়ক ও মহাসড়ক অধিদপ্তর বনাম অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান সিদ্দিকী এবং অন্যান্য এর মামলায় আপীল বিভাগ সংবিধানের ১০৪ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের নাম অন্তর্ভুক্ত করে খতিয়ান সংশোধনের আদেশ প্রদান করে। ভূমিদস্যুদের কাছ থেকে সরকারি সম্পত্তি উদ্ধারেও এই ক্ষমতায় প্রয়োগ করা হয়েছে।
একজন আসামির বয়স বিবেচনায় এবং কনডেম সেলে ৯বছর ধরে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করায় পরবর্তীতে তার সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়। একইভাবে অপর একটি ছেলের কনডেম সেলে ১৪ বছর অতিবাহিত করায় তার সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দন্ডিত করা হয়। একটি মামলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এর ১১ক অনুযায়ী মৃত্যুদন্ড প্রদান করে আদালত এবং হাইকোর্ট বিভাগ সেই রায় বহাল রাখে।
সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে আপিল দায়ের হলে আদালত দেখতে পায় যে- অভিযোগ মতে যৌতুকের জন্য যে মৃত্যু ঘটানো হয়েছে তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি কিন্তু ইহা একটি হত্যাকান্ড যা দণ্ডবিধি ৩০২ ধারা মোতাবেক অপরাধ। আদালত সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের ক্ষমতা প্রয়োগ করে আসামীর সাজা মৃত্যুদণ্ড পরিবর্তন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে কাণ্ডে দণ্ডিত করে।
পরিশেষে তত্ত্বগতভাবে বলা যায় ‘সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার’ এর অর্থ ‘নিখুঁত (complete) ন্যায়বিচার’ নয়; বরং এর অর্থ আরও (Better) ন্যায়বিচার।
লেখক : এস. এম. আরিফ মন্ডল, আইনজীবী, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট। ই-মেইল : mondolarif@yahoo.com