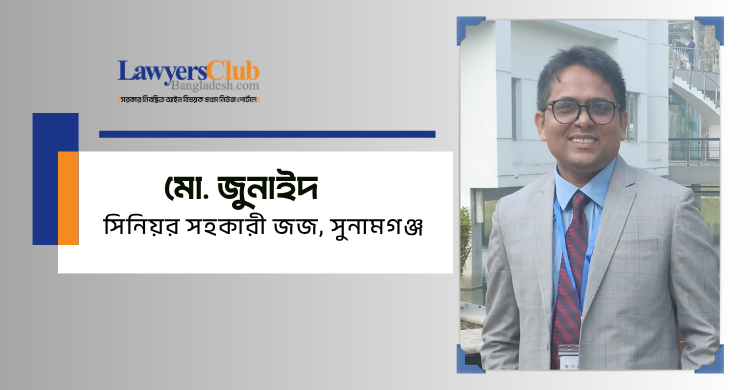মো. জুনাইদ : বাংলাদেশের বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা প্রায়ই ঘোরে কিছু দাবির চারপাশে—আলাদা সচিবালয়, বাজেটের স্বায়ত্তশাসন, বিচারক ও কর্মচারী নিয়োগে বিচার বিভাগের এখতিয়ার, এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি। কেউ কেউ বলেন, এসব কাঠামোগত প্রশ্ন নয়—বিচারকের ব্যক্তিগত সততা ও নৈতিক দৃঢ়তাই আসল স্বাধীনতার উৎস। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে, কাঠামোগত সুরক্ষা ছাড়া ব্যক্তিগত সততা টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব।
চট্টগ্রামে আইনজীবী এবং পরে দেশের চারটি বিভাগের বিভিন্ন জেলায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেখেছি, প্রশাসনিক নির্ভরশীলতা কীভাবে বিচারকের স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আদালতের কর্মী নিয়োগ, বাজেট অনুমোদন, অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, এমনকি বদলি ও পদায়ন—এসব ক্ষেত্রেই নির্বাহী নিয়ন্ত্রণ বিচারকের কাজের পরিসরকে সীমিত করে। ন্যায়বিচারের রক্ষক তখন পরিণত হন প্রশাসনিক শৃঙ্খলার অনুগত অংশে—যেখানে ন্যায়ের চেয়ে আনুগত্য হয়ে ওঠে মুখ্য মানদণ্ড।
এই বাস্তবতায় বিচারবিভাগের আলাদা সচিবালয়, প্রশাসনিক স্বয়ম্ভরতা ও বাজেটের নিজস্বতা কোনো আনুষ্ঠানিক দাবি নয়—এগুলো বিচার বিভাগের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার মৌলিক ভিত্তি। যেমন একটি বৃক্ষের শিকড় গভীর না হলে ঝড়ে টিকে থাকতে পারে না, তেমনি কাঠামোগত ভিত্তি দুর্বল হলে বিচারকের ব্যক্তিগত সততাও স্থায়ী হয় না।
তবে স্বাধীনতা যেন দায়মুক্তির অজুহাত না হয়। জনগণের আস্থা টিকিয়ে রাখতে বিচার বিভাগের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি কাঠামো আরও শক্তিশালী করতে হবে। বিচারকের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন, আচরণবিধি ও নৈতিক তদারকির ব্যবস্থা হতে হবে বিচার বিভাগের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে—বাহ্যিক নয়। বাইরের নিয়ন্ত্রণ স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে, অথচ অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি সেটিকে শৃঙ্খলিত করে।
বিচারকের আত্মিক চেতনা তাঁকে ন্যায়ের পথে অনুপ্রাণিত করে, আর কাঠামোগত স্বাধীনতা তাঁকে সেই পথে নির্ভীকভাবে চলার সুযোগ দেয়। এই দুইয়ের ভারসাম্যেই নিহিত প্রকৃত বিচারিক স্বাধীনতা।
বিচারবিভাগের শক্তি তাই ব্যক্তিগত ত্যাগে নয়, বরং সেই ত্যাগ টিকিয়ে রাখার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায়। আত্মিক চেতনা ও কাঠামোগত শক্তির এই সুষম সমন্বয়ই বিচারবিভাগকে করে তুলতে পারে স্বাধীন, জবাবদিহিমূলক ও জনগণের আস্থার আশ্রয়স্থল।
লেখক : মো. জুনাইদ; সিনিয়র সহকারী জজ, সুনামগঞ্জ।