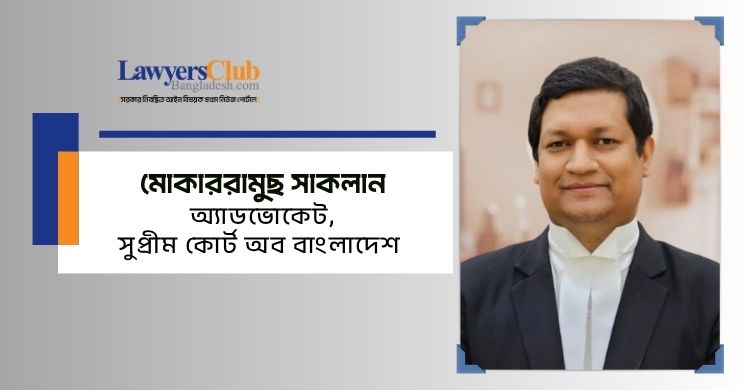মোকাররামুছ সাকলান : আইন কি বলছে? সামরিক সদস্যের বিরুদ্ধে দেওয়ানি পুলিশের একতরফা গ্রেপ্তার কি বৈধ হবে?। নাকি প্রথমেই যেতে হবে কমান্ড চেইনের মাধ্যমে? বাংলাদেশের আইনি কাঠামোয় সামরিক শৃঙ্খলা ও দেওয়ানি এখতিয়ারের সংযোগ সবসময়ই ছিল এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যের বিষয়। এই ভারসাম্য নতুন করে আলোচনায় এসেছে যখন প্রশ্ন উঠেছে যদি কোনো সেনা কর্মকর্তা, যিনি সাময়িকভাবে বেসামরিক প্রশাসনে দায়িত্বপ্রাপ্ত, পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩–এর অধীনে অভিযুক্ত হন, তবে কি তাকে সরাসরি দেওয়ানি পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে? নাকি এই গ্রেপ্তার করতে হবে সেনা কমান্ড কাঠামোর মধ্য দিয়ে?
বাংলাদেশ আর্মি রেগুলেশন ৩৪৬ অনুযায়ী, কোনো সেনা কর্মকর্তা বা সৈনিককে যদি কোনো বেসামরিক দপ্তরে “loaned” বা “placed at the disposal” হিসেবে পাঠানো হয়, তিনি তখনও সামরিক আইনের অধীন থাকেন। বাংলাদেশ আর্মি রেগুলেশন ৩৪৬ এ বলা হচ্ছে “Officers and soldiers whose services are loaned to or placed at the disposal of a civil government or department remain amenable to Military law until they are released from the army and absorbed in that department” অর্থাৎ রেগুলেশনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সিভিল ডিপার্টমেন্টে দায়িত্বে থাকা অবস্থায়ও কর্মকর্তা সামরিক আইনের অধীন থাকবেন এবং সামরিক ঊর্ধ্বতনদের আদেশ পালনে বাধ্য থাকবেন। অর্থাৎ, বেসামরিক প্রশাসনে কাজ করলেও তার আইনি মর্যাদা সামরিক থাকে।
সামরিক আইন ও অপরাধের স্থায়ী দায়
বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট, ১৯৫২-এর ৯২(১) ধারা বলছে যে কোনো ব্যক্তি যখন এই আইনের অধীন অবস্থায় কোনো অপরাধ করে এবং পরে সে সামরিক চাকরি থেকে অব্যাহতি পায়, তবুও তাকে সামরিক হেফাজতে নিয়ে বিচার করা যাবে। এ বিধান স্পষ্ট করে দেয় যে, চাকরি শেষ হলেও অপরাধের দায় থেকে রেহাই নেই। ফলে, বেসামরিক দপ্তরে কাজ করার সময় কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে, তিনি তখনও সামরিক আইনের আওতায় বিচারযোগ্য থাকবেন।
দেওয়ানি পুলিশের গ্রেপ্তার ক্ষমতা
আর্মি অ্যাক্টের ৭৬ ধারা এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়। সেখানে বলা হয়েছে যদি কোনো সামরিক সদস্য আর্মি অ্যাক্টের কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হবার সময় কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কর্মকর্তার এখতিয়ারের মধ্যে থাকেন থাকবেন, তখন উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধিনায়ক বা কমান্ডিং অফিসারের কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে দেওয়ানি পুলিশ তাকে সামরিক হেফাজতে হস্তান্তর করবে। এর মানে হলো, দেওয়ানি পুলিশ সরাসরি কোনো সামরিক কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। বরং সেনা কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুরোধ পেলে তারা সহযোগিতা করতে পারে। এই ধারাটি মুলত সামরিক শৃঙ্খলার মৌলিক সুরক্ষা যা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কাঠামোকে স্থিতিশীল রাখে।
সমান্তরাল এখতিয়ার ও সরকারের চূড়ান্ত ভূমিকা
আর্মি অ্যাক্টের ৯৪–৯৫ ধারা এবং সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন ৩৬৯–৩৭০–এ বলা আছে, যদি কোনো অপরাধ উভয় আদালতে (সামরিক ও দেওয়ানি) বিচারযোগ্য হয়, তাহলে “নির্ধারিত সামরিক কর্তৃপক্ষ” নির্ধারণ করবে কোথায় বিচার হবে। যদি দেওয়ানি আদালত সামরিক সদস্যকে হস্তান্তরের অনুরোধ জানায় এবং সেনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করলে বিষয়টি সরকারের কাছে প্রেরণ করতে পারে, এবং সেখানে সরকারের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র দুই ধরনের শৃঙ্খলা সামরিক কর্তৃত্ব ও দেওয়ানি ন্যায়বিচার এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক অপরাধের মতো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হলেও, সামরিক কর্মকর্তা প্রথমে সেনা আইনের অধীনই থাকবেন যতক্ষণ না সরকার তাকে দেওয়ানি ট্রাইব্যুনালের অধীনে হস্তান্তর করে।
তাহলে প্রশ্ন আসে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের পরোয়ানা: বাস্তবায়ন কীভাবে?
আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩–এর অধীনে ট্রাইব্যুনাল যদি কোনো সামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে, তবে সেটি সরাসরি দেওয়ানি পুলিশ বাস্তবায়ন করতে পারবে না। আইন অনুযায়ী, এই পরোয়ানাটি সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হবে, এবং তারা সামরিক চেইন অব কমান্ড অনুসারে তা কার্যকর করবে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত আছে সংবিধানের ৪৫ অনুচ্ছেদে বর্নিত সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও দেওয়ানি বিচারব্যবস্থার পারস্পরিক সম্মান।
পরিশেষে বলা যায় বাংলাদেশের আইনি কাঠামো একদিকে সেনা শৃঙ্খলার স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধের মতো গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে দেওয়ানি ট্রাইব্যুনালের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে। ফলে, একজন সেনা কর্মকর্তা মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত হলেও, গ্রেপ্তারের পথ একটাই আইনসম্মত সামরিক চ্যানেল। এভাবেই রাষ্ট্রের দুটি প্রধান শৃঙ্খলা সামরিক ও দেওয়ানি আইনের ছায়ায় সমান্তরালভাবে কাজ করে যায়, যেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু শৃঙ্খলা ভঙ্গ না হয়।
দেশের সাধারন মানুষের একটাই প্রত্যাশা ন্যায় বিচার নিশ্চিত দেখতে পাওয়া যাতে করে বিচারব্যবস্থা ও সশস্ত্র বাহিনীর পারস্পরিক সম্মান অক্ষুন্ন থাকে যাতে প্রকৃত দোষীদের সঠিক বিচার হয়।
বি:দ্র: এটি একটি আইনী বিশ্লেষনমূলক আলোচনা। যে কেউ এর সাথে দ্বিমত করতে পারেন। মনে রাখবেন আইন বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যখ্যা দেবেন আদালত। আর আদালতের আদেশ সকলের জন্য অবশ্য পালনীয়।
লেখক : মোকাররামুছ সাকলান; অ্যাডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট অব বাংলাদেশ।